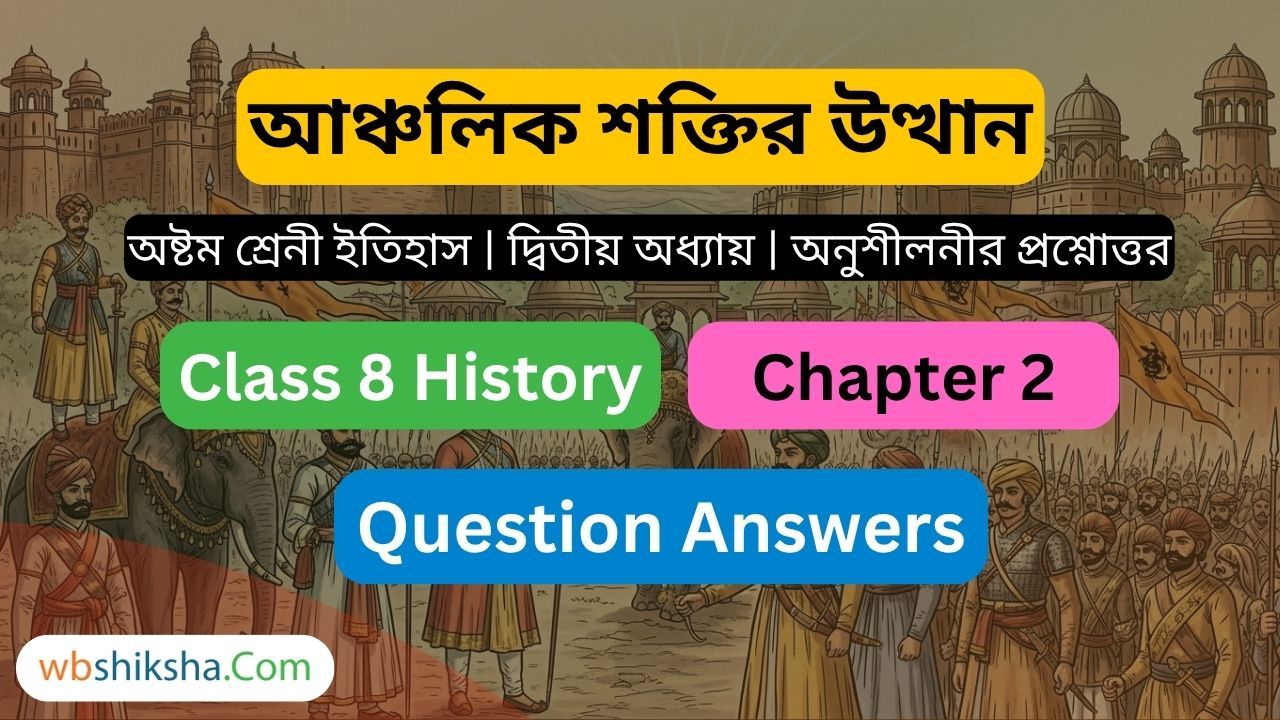প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই আর্টিকেলে আমরা Class 8 History Chapter 2 Question Answer নিয়ে এসেছি। তোমাদের অষ্টম শ্রেনীর ইতিহাস পাঠ্য বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভেবে দেখো খুঁজে দেখো অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর এখানে সহজ ও সরল ভাষায় লিখে দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর নীচে যুক্ত করা হয়েছে আশা করি সবার ভালো লাগবে।
আঞ্চলিক শক্তির উত্থান
অষ্টম শ্রেনী ইতিহাস | দ্বিতীয় অধ্যায়
Class 8 History Chapter 2 Question Answer | আঞ্চলিক শক্তির উত্থান প্রশ্ন উত্তর
ভেবে দেখো খুঁজে দেখো প্রশ্ন উত্তর
১। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :
উত্তর :
| ক-স্তম্ভ | খ-স্তম্ভ |
| অযোধ্যা | সাদাৎ খান |
| ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ | বক্সারের যুদ্ধ |
| স্বত্ববিলোপ নীতি | লর্ড ডালহৌসি |
| লাহোরের চুক্তি | প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ |
| টিপু সুলতান | মহীশূর |
২। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :
ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার – (দেওয়ান / ফৌজদার/নবাব)।
উত্তর : দেওয়ান।
খ) আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন— (মারাঠা / আফগান/ পারসিক)।
উত্তর : আফগান।
গ) আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল – (মির জাফর ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/মির কাশিম ও ব্রিটিশ কোম্পানিরমধ্যে)।
উত্তর : সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে।
ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন— (সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম/সম্রাট ফাররুখশিয়র/ সম্রাট ঔরঙ্গজেব)।
উত্তর : সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম।
ঙ) স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন— (টিপু সুলতান / সাদাৎ খান/নিজাম)।
উত্তর : নিজাম।
৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :
ক) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কি ছিল?
উত্তর : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফারুখশিয়র একটি আদেশ বা ফরমান জারি করেন।এতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। যা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, –
১. ব্রিটিশ কোম্পানি বছরে মাত্র ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে। কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না।
২. কোম্পানির পণ্য কেউ চুরি করলে তাকে বাংলার নবাব শাস্তি দেবেন ও কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেবেন।
৩. কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে অনুমতি পত্র থাকলেই জাহাজ অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে।
৪. বাংলার নবাবের মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল প্রয়োজন মতো কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে।
খ) কে, কীভাবে ও কবে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
উত্তর :
কে প্রতিষ্ঠা করে?: হায়দ্রাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি ।
কীভাবে ও কবে?: হায়দরাবাদ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশ। এখানে মুঘল প্রাদেশিক শাসক মুবারিজ খান স্বাধীন শাসকের মতো শাসন করতেন। ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে মুঘল দরবারের শক্তিশালী অভিজাত মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি তাকে পরাজিত করেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে হায়দরাবাদে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।এরপর ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিজাম শাসিত স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে।
গ) ‘পলাশির লুণ্ঠন’ কাকে বলে ?
উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জুন ব্রিটিশ কোম্পানির বাহিনী নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হারিয়ে মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান ।বস্তুত নবাব মিরজাফরকে সহায়তা করার বিনিময়ে ব্রিটিশ কোম্পানি অবাধে সম্পদ হস্তাগত করতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজের কলকাতা আক্রমণের অজুহাতে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নেয় কোম্পানি।তার উপরে ক্লাইভ সহ কোম্পানির উচ্চ পদাধিকারীরা মিরজাফরের থেকে প্রচুর সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছিল।সব মিলিয়ে পলাশির যুদ্ধের পরে প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পদ মিরজাফরের থেকে আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানি। কোম্পানির তরফে এই অর্থ আত্মসাৎকে পলাশীর লুণ্ঠন বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কোষাগার এই লুণ্ঠনের ফলে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।
ঘ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?
উত্তর : কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলায় এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কায়েম হয়।বাস্তবে বাংলায় দুজন শাসক তৈরি হয়।যাবতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়ে গিয়েছিল নবাব নজম উদ – দৌলার উপর।অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। ফলে নবাবের হাতে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব।ব্রিটিশ কোম্পানি পেয়েছিল দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাংলার এই শাসন ব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলে ।
ঙ) ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের কাজ কী ছিল ?
উত্তর : ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক অঞ্চলেই ব্রিটিশ কোম্পানি ‘পরোক্ষ শাসন’ চালাত।নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি রাখত কোম্পানি। সেই প্রতিনিধিরা রেসিডেন্ট নামে পরিচিত ছিল।
কোম্পানির নজর এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ভারতীয় রাজশক্তিগুলির বিশেষ ছিল না। কোম্পানির হয়ে সেই নজরদারির কাজটাই চালাত স্থানীয় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট।
৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :
ক) অষ্টাদশ শতকে ভারতে প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতাই কেবল দায়ী ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর : অষ্টাদশ শতকে ভারতের প্রধান প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে মুঘল সম্রাটদের ব্যাক্তিগত অযোগ্যতাকে দায়ী করা হয়।তবে একটা সাম্রাজ্য তথা শাসনব্যবস্থা শুধু ব্যক্তি – সম্রাটের দক্ষতা – যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না।তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।এক্ষণে ভারতের আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে । যথা,-
১. দুর্বল শাসন কাঠামো: সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহ জাহানের সময় থেকেই মুঘল শাসন কাঠামোয় ছোটোবড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলে সেই দুর্বলতাগুলো আরও বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।
২. সামরিক ব্যবস্থার অবনতি: বিশেষ কোনো সামরিক সংস্কার অষ্টাদশ শতকের মুঘল সম্রাটরা করেনি। ফলে সাম্রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহ ও বাইরের আক্রমণ মোকাবিলা করতে সামরিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়।
৩. জায়গির ও মনসবদারি ব্যবস্থার সংকট: এই সময় ভূমি রাজস্বের হিসেবে নানা গরমিল দেখা যায়। এর নেতিবাচক প্রভাব সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উপরেও পড়ে।এছাড়া ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।
৪. কৃষক বিদ্রোহ: সাম্রাজ্যের আয় – ব্যয়ের গরমিল বাস্তবে চাপ তৈরি করেছিল কৃষি ব্যবস্থার উপর।সেই চাপের বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় ৷
পরিশেষে বলা যায় উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল।এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ঘটে।
খ) পলাশির যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোনটি ব্রিটিশ কোম্পানির ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও ।
উত্তর: ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজদের উত্তরণ ঘটে।বাংলার নবাব ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।তবে পলাশির যুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারে পলাশির যুদ্ধের থেকে বক্সারের যুদ্ধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।এর কারণগুলি হল,-
১. বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীন নবাবের অবসান ঘটে।
২. বক্সারের যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়।
৩. বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তাছাড়া অযোধ্যার শাসকের পরাজয়ের ফলে পুরো উত্তর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়।
৪. বক্সারের যুদ্ধ ভারতীয় রাজাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়।ফলে সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।
৫. বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলার বুকে একচেটিয়া শোষণ ও লুণ্ঠন শুরু করে। ফলে বাংলার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে।
পরিশেষে বলা যায় পলাশির যুদ্ধের জেতার পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তারের যে বীজ বপন করেছিল বক্সারের যুদ্ধের পর তা অঙ্কুরিত হয়ে ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়।
গ) মীর কাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার কী ভূমিকা ছিল? বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব কী হয়েছিল?
উত্তর :
ব্যক্তিগত ব্যবসার ভূমিকা: প্রথমদিকে ব্রিটিশ কোম্পানি মির কাশিমের পদক্ষেপগুলি নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মির কাশিমের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ শুরু হয়। কারণ,-
১. কোম্পানির বণিকদের তরফে বেআইনি ব্যবসার ফলে বাংলার অর্থনীতি সমস্যার মুখে পড়েছিল।
২. একদিকে কোম্পানির শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় নবাবের প্রাপ্য রাজস্বে ঘাটতি পড়েছিল। আবার,
৩. অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছিল।
– তাছাড়া অন্যান্য বিদেশি বণিক গোষ্ঠীও ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নবাবের কাছে নালিশ জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নবাব দেশীয় বণিকদের উপর থেকেও বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেন। ফলে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় বণিকরা রক্ষা পেলেও নবাবি কোশাগার অর্থসংকটের মুখে পড়ে।
দ্বৈত শাসনের প্রভাব: বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়-
১. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলায় দুজন শাসক তৈরি হয়। রাজনৈতিক ও নিজামতের দায়িত্ব ছিল বাংলার নবাবের হাতে। অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি।
২. নবাবের হাতে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে ছিল দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা।
৩. ক্রমে দেখা যায় নিজেদের বাণিজ্য চালানোর প্রয়োজনে ব্রিটিশ কোম্পানির ব্রিটেন থেকে মূলধন নিয়ে আসার পরিমান হ্রাস পেতে থাকে। বাংলার রাজস্বই কোম্পানির ব্যবসায় লগ্নি করা হয়।
৪. এই সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। এর ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।
পরিশেষে বলা যায় বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল।
ঘ) ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি থেকে স্বত্ববিলোপ নীতিতে বিবর্তনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
উত্তর : ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন বিস্তার প্রক্রিয়ায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ত্ববিলোপ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজ শক্তিগুলির মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব চলত। প্রত্যেকেই নিজের শাসন এলাকা ও সম্পদ বাড়াবার উদ্যোগ নিত।ফলে পারস্পরিক সংঘাত ছিল অনিবার্য। তাই ক্রমেই আঞ্চলিক রাজনীতির ব্যাপারে ব্রিটিশ কোম্পানি ভূমিকা নিতে শুরু করে। দেশীয় রাজশক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির আগ্রাসী নীতির অন্যতম রূপ ছিল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি। লর্ড ওয়েলেসলি ওই নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের আঞ্চলিক শক্তিগুলির বিবাদজনিত অশান্তিকে ওয়েলেসলি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপদ হিসেবে তুলে ধরতেন। তারপর সরাসরি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশীয় শক্তিগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য করতেন।
অপরদিকে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। এই নীতির প্রয়োগ কর্তা লর্ড ডালহৌসীর আমলে কোম্পানির আগ্রাসী রূপ প্রকট হয়েছিল। যেসব ভারতীয় শাসকদের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকত না তাদের শাসন এলাকা কোম্পানির হস্তাগত হয়ে যেত। সেভাবেই ডালহৌসি সাঁতরা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন। এইভাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লর্ড ডালহৌসির নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশের ৬০ ভাগেরও বেশি অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।
ঙ) মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দি খান এর সময়ে বাংলার সঙ্গে মুঘল শাসনের সম্পর্কের চরিত্র কেমন ছিল?
উত্তর :
মুর্শিদকুলি খানের আমল: মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলায় একদল ক্ষমতাবান জমিদারশ্রেণি তৈরি হয়। তাঁরা নাজিমকে নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার বদলে নিজেদের অঞ্চলে ক্ষমতা ভোগ করতেন। মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসার পক্ষে অনুকূল ছিল। স্থল ও সমুদ্রপথে নানান দ্রব্য সুবা বাংলা থেকে রপ্তানি করা হতো। হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনীয় বণিকরাই ওই ব্যবসায় প্রভাবশালী ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে উমিচাঁদ ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজিদ ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। এইসব ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। শাসকেরা এদের সহায়তার ওপর নির্ভর করত। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মূলধন বিনিয়োগকারী জগত শেঠের নাম করা যায়। সুবা বাংলার কোশাগার ও টাকশাল জগত শেঠের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলত।
আলিবর্দি খানের আমল: আলিবর্দি খানের শাসনকালে মুঘলদের হাত থেকে সুবা বাংলার অধিকার বেরিয়ে যায়। শাসনতান্ত্রিক কোনো খবরাখবরই দিল্লির মুঘল সম্রাটকে জানানো হতো না। তাছাড়া নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোর ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। যদিও মুঘল কর্তৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হতো । তবুও বাংলা, বিহার উড়িষ্যায় আলিবর্দি কার্যত একটি স্বশাসিত প্রশাসন চালাতেন।
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর
১. মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কবে মারা যান?
উত্তর : ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে।
২. পলাশির যুদ্ধ কবে হয়?
উত্তর :১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন।
৩. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান ঘটে?
উত্তর :পলাশির যুদ্ধ।
৪. মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে পাঠিয়েছিলেন কে?
উত্তর : ঔরঙ্গজেব।
৫. দেওয়ান পদে মুর্শিদকুলি খানকে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করেন কে?
উত্তর : সম্রাট ফাররুখশিয়র।
৬. কত খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার নাজিমপদ দেওয়া হয়?
উত্তর : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে।
৭. জগৎ শেঠ কী?
উত্তর : জগৎশেঠ নির্দিষ্ট একটি বণিক পরিবারের উপাধি।
৮. মুর্শিদকুলি খান কবে মারা যান?
উত্তর :– ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে।
৯. আলিবর্দি খান কবে মারা যায়?
উত্তর : ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে।
১০. আলিবর্দি খানের পরে কে বাংলার নবাব হয়?
উত্তর : সিরাজ উদ দৌলা।
১১. সিরাজ উদ – দৌলা আলিবর্দি খানের কে?
উত্তর : দৌহিত্র (কন্যার পুত্র বা নাতি)
১২. বর্গিহানা কাকে বলে?
উত্তর : ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্গি বা মারাঠারা বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ ও আক্রমণ চালিয়েছিল। এই আক্রমণকেই বলে বর্গিহানা।
১৩. কে, কাকে কুলিচ খান উপাধি দেন?
উত্তর : সম্রাট ঔরঙ্গজেব, মির কামার উদ – দিন খান সিদ্দিকিকে কুলিচ খান উপাধি দেন।
১৪. সম্রাট ফাররুখশিয়র মির কামার উদ দিন খান সিদ্দিকিকে কী উপাধি দেন?
উত্তর : নিজাম – উল – মুলক।
১৫.সম্রাট মহম্মদ শাহ মির কামার উদ দিন খান সিদ্দিকিকে কী উপাধি দেন?
উত্তর : আসফ ঝাল
১৬. কে কবে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তর : মির – কামার উদ্দিন খান সিদ্দিকি বা আসফ ঝা বা নিজাম – উল – মুলক ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।
১৭. কে কবে মুবারিজ খানকে হারায়?
উত্তর : আসফ ঝা, ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে।
১৮. কবে কার নেতৃত্বে অযোধ্যা স্বশাসিত আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়?
উত্তর : ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে, সাদাৎ খানের নেতৃত্বে।
১৯. কত খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খান মারা যায়?
উত্তর : ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে।
২০. কে কাকে বুরহান – উল মুলক উপাধি দেয়?
উত্তর : মহম্মদ শাহ, সাদাৎ খানকে।
২১. কত খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খান মারা যায়?
উত্তর : ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে।
২২. সফদর জং কত খ্রিস্টাব্দে মারা যায় ?
উত্তর : ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে।
২৩. সফদর জং মারা যাবার পর বাংলার শাসক কে হয়?
উত্তর : সুজা – উদ দৌলা।
২৪. কত খ্রিস্টাব্দে ফাররুখশিয়রের ফরমান জারি হয়?
উত্তর : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে।
২৫. ফাররুখাশয়রের ফরমান কী?
উত্তর : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র একটি আদেশ বা ফরমান জারি করে। এই ফরমান মোতাবেক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। একে ফাররুখশিয়রের ফরমান বলে।
২৬. ফাররুখশিয়রের ফরমানে কী কী বলা হয়?
উত্তর :
১. ব্রিটিশ কোম্পানি বছরে মাত্র ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে।
২. এর জন্য কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না ।
৩. কোম্পানি কলকাতার কাছাকাছি ৩৮ টি গ্রামে জমিদারি কিনতে পারবে।
৪. কোম্পানির পণ্য কেউ চুরি করলে বাংলার নবাব তাকে শাস্তি দেবেন ও কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেবেন।
৫. কোম্পানির জাহাজের সাথে অনুমতিপত্র থাকলে সে অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে।
৬. বাংলার নবাবের টাকশাল প্রয়োজন মতো কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে।
২৭. বক্সি শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : সেনাপতি।
২৮. সিরাজ উদ দৌলার ব্রিটিশ বিরোধের কয়েকটি কারণ লেখো।
উত্তর : ১. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা অনুমতিতে বাদশাহী সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল যা বাদশাহী সাম্রাজ্যের নিয়ম বিরুদ্ধ।
২. কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে ‘দস্তক’ পেয়েছিল তার অপব্যবহার করছিল। এতে দেশীয় শুল্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল
৩. যে সকল বাদশাহী কর্মচারী নিজের লাভের জন্য বাদশাহী কর্মকাণ্ডের ক্ষতি করছে ইংরেজরা তাদের দলে টানছিল।
২৯. অন্ধকূপ হত্যা কী?
উত্তর : হলওয়েল প্রচার করেন সিরাজ উদ দৌলা ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন যখন কলকাতা দখল করে তখন তিনি নাকি ১৪৬ জন ব্রিটিশ নরনারীকে একটি ছোটো ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন। এর ফলে অনেক বন্দি মারা যায়। এই ঘটনা ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামে পরিচিত। তবে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র হলওয়েলের এই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করেন।
৩০. কত খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি হয়?
উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানির সাথে সিরাজ উদ দৌলার।
৩১. পলাশির লুন্ঠন কাকে বলে?
উত্তর : পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজের কলকাতা আক্রমণের অজুহাতে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নেয় কোম্পানি। তার উপরে ক্লাইভ সহ কোম্পানির উঁচু পদাধিকারীরা মির জাফরের থেকে প্রচুর সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছিল। সব মিলিয়ে পলাশির যুদ্ধের পর প্রায় 3 কোটি টাকার সম্পদ মির জাফরের থেকে আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানি। কোম্পানির তরফে এই অর্থ আত্মসাৎকে পলাশির লুন্ঠন বলে।
৩২. মির কাশিম রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের বদলে কোন জায়গায়কে বেছে নিয়েছিল?
উত্তর : মুঙ্গেরকে।
৩৩. মির কাশিমের ইংরেজদের বিরোধিতার কারণ লেখো।
উত্তর : ইংরেজদের আনুগত্যে সিংহাসনে বসলেও যে যে কারণে মির কাশিম ইংরেজদের বিরোধিতা করে ও তাদের মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেগুলি হল,-
১. কোম্পানির বণিকদের তরফে বেআইনি ব্যবসার ফলে বাংলার অর্থনীতি সমস্যার মুখে পড়েছিল।
২. কোম্পানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় নবাবের প্রাপ্য রাজস্বে ঘাটতি পড়েছিল।
৩. দেশীয় বণিকেরা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় অসম প্রতিযোগিতার মুখে পিছিয়ে পড়ছিল।
৪. অন্যান্য বিদেশি বণিক গোষ্ঠীও ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নবাবের কাছে নালিশ জানায়।
– উপরিউক্ত কারণগুলোর ফলস্বরূপ মির কাশিম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতা করে ও তাদের মধ্যে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
৩৪. বক্সারের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মির কাশিমের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।
৩৫. বক্সারের যুদ্ধে কে কে মির কাশিমের সঙ্গ দিয়েছিল?
উত্তর : অযোধ্যার শাসক সুজা উদ দৌলা ও দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম।
৩৬. বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করো। / বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো।
উত্তর : ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মির কাশিমের যৌথ বাহিনী ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংঘটিত হওয়া বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যথা,-
১. বক্সারের যুদ্ধ জয়ের পর বাংলার উপর কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়েছিল।
২. অযোধ্যার শাসকের পরাজয়ের ফলে পুরো উত্তর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়।
৩. দিল্লির মুঘল সম্রাটকে হারিয়ে দেওয়ায় আনুষ্ঠানিক মুঘল সার্বভৌমত্ব ও সমস্যার মুখে পড়ে।
৪. পরাজয়ের ফলে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অধিকার দিতে বাধ্য হন।
– পরিশেষে বলা যায় পলাশির যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধ জয়ে তা আরও সফল হয়।
৩৭. দেওয়ানি অধিকার কী?
উত্তর : বাদশাহ শাহ আলম দিল্লির অধিকার ফিরে পাওয়ার বদলে একটি ফরমান জারি করেন। সেই ফরমান অনুযায়ী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে দেওয়া হয়। তার বদলে কোম্পানি শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে।
৩৮. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কাকে বলে?
উত্তর : কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর বাংলায় এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কায়েম হয়। বাস্তবে বাংলায় দুজন শাসক তৈরি হয়। রাজনৈতিক ও নিজামতের দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। আর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। অর্থাৎ নবাবের হাতে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব। ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে ছিল দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা। বাংলার এই শাসন ব্যবস্থাকে বলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা।
৩৯. বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কী প্রভাব পড়েছিল?
উত্তর : দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
৪০. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কবে হয়েছিল?
উত্তর : ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে।
৪১. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ লেখো।
উত্তর : ১. ব্রিটিশ কোম্পানির অতিরিক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা।
২. খরার প্রভাবে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।
৩. জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকা।
৪. মহামারী প্রকোপ
– প্রভৃতি কারণে ১৭৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
৪২. ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কারা?
উত্তর : নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি রাখত কোম্পানি। সেই প্রতিনিধিরা রেসিডেন্ট নামে পরিচিত।
৪৩. ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাজ কী ছিল?
উত্তর : কোম্পানির নজর এড়িয়ে যাতে ভারতীয় রাজশক্তিগুলি স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারে সে বিষয়ে দেখাশোনা করা ছিল ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাজ।
৪৪. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন?
উত্তর : লর্ড ওয়েলেসলি।
৪৫. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কী?
উত্তর : ব্রিটিশ কোম্পানির আগ্রাসী নীতির অন্যতম রূপ ছিল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি। এই নীতির প্রবর্তন করেন লর্ড ওয়েলেসলি। এই নীতিতে বলা হয় যদি কোনো দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশদের সঙ্গে মিত্রতা করে তবে ওই রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি বহন করবে।
৪৬. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তগুলো লেখো।
উত্তর : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তগুলো হল,-
১. এই নীতি গ্রহণকারী রাজ্যের রাজসভায় একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকবে।
২. এই নীতি গ্রহণকারী রাজ্যে একদল ব্রিটিশ সেনা থাকবে যাদের খরচ ওই রাজ্যকেই বহন করতে হবে।
৩. কোম্পানির পরামর্শ ছাড়া ওই রাজ্য অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বা মিত্রতা করতে পারবে না।
৪৭. কে স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেয়?
উত্তর : হায়দ্রাবাদের নিজাম।
৪৮. ইঙ্গ – মহীশূর যুদ্ধ কাকে বলে?
উত্তর : ১৭৬৭ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারটি যুদ্ধ হয় কোম্পানি ও মহীশূরের মধ্যে। সেগুলিকে ইঙ্গ – মহীশূর যুদ্ধ বলে।
৪৯. দুপ্লে কে ছিলেন?
উত্তর : পন্ডিচেরির ফরাসি গভর্নর জেনারেল।
৫০. চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ কবে হয়?
উত্তর : ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে।
৫১. কবে কাদের মধ্যে সলবাইয়ের চুক্তি হয়?
উত্তর : ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে, মারাঠাদের সাথে ব্রিটিশ ইস্টে ইন্ডিয়া কোম্পানির।
৫২. কবে কাদের মধ্যে বেসিনের সন্ধি হয়?
উত্তর : ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এর সাথে ব্রিটিশ কোম্পানির।
৫৩. কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ হয়?
উত্তর : ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে।
৫৪. কত খ্রিস্টাব্দে লাহোর চুক্তি হয়?
উত্তর : ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে।
৫৫. স্বত্ববিলোপ নীতি কী?
উত্তর : সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬- খ্রিস্টাব্দ) সাম্রাজ্য বিস্তারের পন্থা হিসেবে স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতি অনযায়ী যেসব ভারতীয় শাসকদের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী নেই, তাদের শাসন এলাকা কোম্পানির হস্তাগত হয়ে যেত। এই নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসি সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন।
আরো পড়ুন
Class 8 History Chapter 3 Question Answer | ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রশ্ন উত্তর
Note: এই আর্টিকেলের ব্যাপারে তোমার মতামত জানাতে নীচে দেওয়া কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো। ধন্যবাদ।