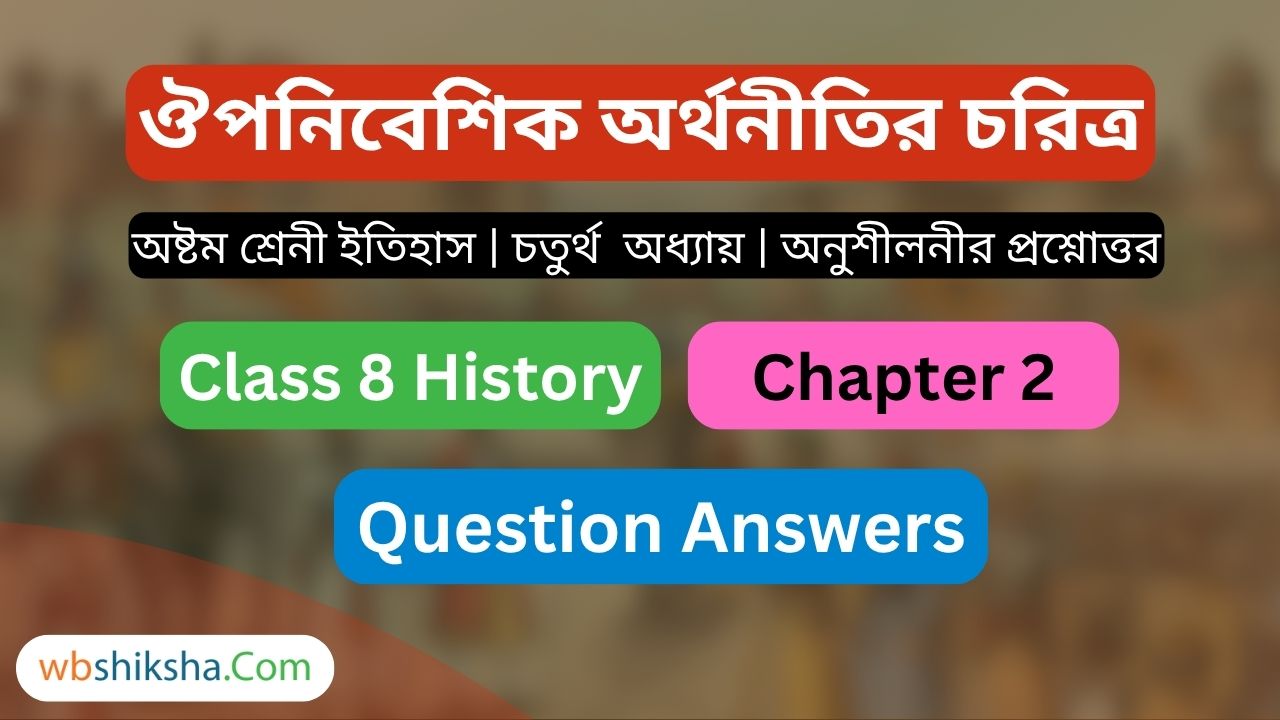প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই আর্টিকেলে আমরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র প্রশ্ন উত্তর নিয়ে এসেছি। তোমাদের অষ্টম শ্রেনীর অতীত ও ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাস পাঠ্য বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে ভেবে দেখো খুঁজে দেখো অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর এখানে সহজ ও সরল ভাষায় লিখে দেওয়া হয়েছে।
ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র
অষ্টম শ্রেনী ইতিহাস | চতুর্থ অধ্যায়
ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র প্রশ্ন উত্তর | Class 8 History Oponibesik Arthonitir charitra Question Answer
ভেবে দেখো খুঁজে দেখো প্রশ্ন উত্তর
১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :
ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন – (হেস্টিংস/ কর্নওয়ালিস/ ডালহৌসি)।
উত্তর : কর্নওয়ালিস।
খ) মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল – (বাংলায়/ উত্তর ভারতে / দক্ষিণ ভারতে)।
উত্তর : উত্তর ভারতে।
গ) ‘দাদন’ বলতে বোঝায় – (অগ্রিম অর্থ / আবওয়াব / বেগার শ্রম)।
উত্তর : অগ্রিম অর্থ।
ঘ) ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম পাটের কারখানা চালু হয়েছিল – (রিষড়ায়/ কলকাতায়/ বোম্বাইতে)।
উত্তর : রিষড়ায়।
ঙ) দেশের সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়াকে বলে – (সম্পদের বহির্গমন/ অবশিল্পায়ন/ বর্গাদারি ব্যবস্থা)।
উত্তর : সম্পদের বহির্গমন।
২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :
ক) ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়।
উত্তর : ভুল।
খ) নীল বিদ্রোহ হয়েছিল মাদ্রাজে।
উত্তর : ভুল।
গ) দাক্ষিণাত্যে তুলো চাষের সঙ্গে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বিষয় জড়িত ছিল।
উত্তর : ঠিক।
ঘ) রেলপথের বিস্তারের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল।
উত্তর : ভুল।
ঙ) টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কোম্পানি-শাসনের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছিল।
উত্তর : ঠিক।
৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০ – ৪০টি শব্দ) :
ক) ‘সূর্যাস্ত আইন’ কাকে বলে ?
উত্তর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা অন্যতম শর্ত ছিল বছরের নির্দিষ্ট দিনে, সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে প্রত্যেক জমিদারদের প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানির কাছে জমা দিতে হবে।নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে ওই জমিদারদের সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার কোম্পানির ছিল। এই ব্যবস্থা সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত।
খ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝো?
উত্তর : কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে বোঝায় নিজ ব্যবহারের পরিবর্তে বাণিজ্যের জন্য ফসল উৎপাদন করা । ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে এটি শুরু হয়েছিল।এর ফলে বাণিজ্যের কাজে প্রয়োজন বিভিন্ন ফসলের গুরুত্ব বেড়েছিল।যেমন, চা, নীল, পাট, তুলো প্রভৃতি।
গ) ‘দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা’ কেন হয়েছিল?
উত্তর : ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের প্রভাবে কার্পাস তুলোর চাহিদা বাড়লে দাক্ষিণাত্যে কার্পাসের চাষ বাড়তে থাকে।কিন্তু গৃহযুদ্ধ থেমে গেলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুলোর দাম একদম কমে যায়।সেই সময় অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ, একইসাথে খরা ও অজন্মার ফলে কৃষক সমাজ দুর্দশার মুখে পড়ে।এই সুযোগে স্থানীয় সাহুকরেরা কৃষকদের ঋণ দেওয়ার নামে উৎপন্ন ফসলের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করত।এর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের তুলো চাষিরা বিদ্রোহ করে।যা ‘দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা’ নামে পরিচিত।
ঘ) সম্পদের বহির্গমন কাকে বলে?
উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতের বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করে।তার পরিবর্তে ভারতের কোনো অর্থনৈতিক উন্নতি করেনি।এইভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হওয়াকেই ‘সম্পদের বহির্গমন’ বলে।বাস্তবে ভারতে সম্পদ বহির্গমনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন স্পঞ্জের মতো কাজ করত । ভারত থেকে সম্পদ শুষে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হত ।
ঙ) অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝো?
উত্তর : অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদিত হয়।এই বিদেশি পণ্য ভারতের বাজারে ছেয়ে যায়।অত্যন্ত সস্তা দামে বিদেশি পণ্যের আমদানি শুরু হলে দেশীয় শিল্প পিছিয়ে পড়ে। দেশীয় শিল্পের এই অবনতি তথা ধ্বংসের প্রক্রিয়াকেই অবশিল্পায়ন বলে । যেমন ব্রিটেনে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্প ক্রমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :
ক) বাংলার কৃষক সমাজের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয় ?
উত্তর : ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির তরফে জমিদারদের সঙ্গে খাজনা আদায় বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমি জমিদারি সম্পত্তি হয়ে পড়ে। বাংলায় কৃষক সমাজের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। যেমন,-
(i) কৃষকের অবস্থার অবনতি: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের সমৃদ্ধি বাড়লেও কৃষকের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। কৃষকরা জমিদারদের অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন।
(ii) কৃষকের জমি দখলি স্বত্ব খারিজ: প্ৰাক্- ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকেরও জমির উপর দখলি স্বত্ব ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকের স্বত্বকে খারিজ করে তাদের প্রজায় পরিণত করা হয়।
(ii) অতিরিক্ত কর: উঁচু হারে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপত। তাছাড়া প্রায়ই নানান আবওয়াব বা বেআইনি কর আদায় করা হতো কৃষকদের থেকে।
(iv) কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত: নির্দিষ্ট খাজনা দিতে না পারলে কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও জমিদারকে দেওয়া হয়।
– পরিশেষে বলা যায় বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে কোম্পানির কর্তৃত্ব ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে দৃঢ় হয়েছিল এই ব্যবস্থার ফলে নানা দিক থেকে চাপে পড়ে কৃষকের অবস্থার অবনমন হতে থাকে।
খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্ত গুলির তুলনামূলক আলোচনা করো। তিনটির মধ্যে কোনটি কৃষকদের জন্য কম ক্ষতিকারক বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দিয়ে লেখো।
উত্তর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রায়তওয়ারি, মহলওয়ারি, বন্দোবস্তগুলির তুলনামূলক আলোচনা –
(i) বন্দোবস্তের এলাকা: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চালু হয়েছিল।
➤ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে।
➤ মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকায়।
(ii) রাজস্ব আদায়: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানির রাজস্ব আদায় করত জমিদারের কাছ থেকে।
➤ রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করত সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে।
➤ মহলওয়ারি বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার মহলের জমিদার বা প্রধানের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন।
(iii) খাজনার হার: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঔপনিবেশিক সরকার জমিদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর নিতেন আর জমিদার নিজের ইচ্ছেমতো কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত নির্দিষ্ট কোনো খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করা ছিল না ।
➤ রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে খাজনার হারে সমতা ছিল না কোথাও ৪৫ শতাংশ কোথাও ৫৫ শতাংশ খাজনা নেওয়া হতো।
➤ মহলওয়ারি বন্দোবস্তেও উঁচু হারে রাজস্ব ধার্য করা হতো।
কোনটা কম ক্ষতিকর?: আমার মতে এই তিনটি ভূমি বন্দোবস্তের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকের পক্ষে কম ক্ষতিকর ছিল। কারণ –
(i). চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনার হার ছিল কম।
(ii). এই বন্দোবস্তে কিছু মহানুভব জমিদার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।
– তবে পরিশেষে বলা যায় এই তিনটি বন্দোবস্তই কৃষকদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
গ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষক-অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কী সরাসরি সম্পর্ক ছিল? সেই নিরিখে ‘দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা’ কে তুমি কীভাবে বিচার করবে?
উত্তর :
✳️ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষক:-
অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সম্পর্ক: ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতির আরেকটি দিক ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। অর্থাৎ বাণিজ্যের কাজে প্রয়োজন বিভিন্ন কৃষিজ ফসল চাষের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব পড়েছিল। এই কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে ভারতের কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সম্পর্ক ছিল। কারণ –
(i) কৃষকদের মধ্যে ভেদাভেদ: কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভারতীয় কৃষক সমাজে পারস্পরিক ভেদাভেদ তৈরি হয়েছিল।
(ii) মুনাফা লাভ না হওয়া: কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষির উন্নতি যা হতো তাতে কৃষকের সরাসরি লাভ বিশেষ হতো না। মূলধন বিনিয়োগকারীরাই বেশিরভাগ মুনাফা করতেন।
(iii) নীলকরদের অত্যাচার: পূর্ব ভারতে নীলকররা জোর করে অগ্রিম টাকা বা দাদন দিয়ে চাষিদের বাধ্য করতো নীল চাষ করতে। এর ফলে নীলকরদের প্রতি চাষিদের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়।
✳️দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা বিষয়ে আমার মতামত:-
আমার মতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য যে কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলাফলই দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা। কারণ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রভাবে কার্পাস তুলোর চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলে দাক্ষিণাত্যে কার্পাস তুলোর চাষ বেড়ে যায়। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর দাক্ষিণাত্যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুলোর দাম একদম কমে যায়। তার উপর চড়া হারে রাজস্বের চাপ ছিল। এমত পরিস্থিতিতে সাহুকর ও মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে কৃষকরা বিদ্রোহ শুরু করে।
ঘ) বাংলার বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যনীতির কী ধরনের সম্পর্ক ছিল ? কেন দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি তৈরি করেন ভারতীয়রা?
উত্তর :
✳️ বাংলা বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে:-
কোম্পানির বাণিজ্য নীতির সম্পর্ক: বাংলার বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্য নীতির সম্পর্ক মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। কারণ, –
(i) ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ব্রিটেনে সুতির কাপড় ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্য কাপড় আমদানির উপরেও চড়া শুল্ক চাপানো হয়েছিল।
(ii) বাংলার তাঁতিদের সস্তায় দ্রব্য বিক্রি করতে এবং কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দাম মেনে নিতে বাধ্য করা হতো। এর ফলে তাঁত শিল্পে ক্ষতি হতে শুরু হয়।
(iii) বাংলার হস্তশিল্পীদের তৈরি জিনিস যাতে বেশি দামে কেনা না হয় তার জন্যও নজরদারি রাখত ব্রিটিশ কোম্পানি।
(iv) বাংলার তাঁতিদের চড়া দামে কাঁচা সুতো কিনতে হতো। চড়া দামে কাঁচামাল কেনা ও সস্তা দামে তৈরি দ্রব্য বিক্রিতে বাধ্য করা হতো।
– এভাবে কোম্পানির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার বস্ত্র শিল্প ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।
✳️ দেশীয় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি:-
গড়ে তোলার কারণ: ঔপনিবেশিক সরকার শিল্পগুলিকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। তবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা সেই সহযোগিতা পাননি । কেবল সুতির কাপড় তৈরির শিল্পে অনেক ভারতীয় বিনিয়োগকারী ছিল। ব্যাংক থেকে ধার পাওয়ার অথবা ব্যাংকের সুদের হারের ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। একারণে ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।
ঙ) ভারতে কোম্পানি-শাসন বিস্তারের প্রেক্ষিতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা করো।
উত্তর : ভারতে কোম্পানির শাসন বিস্তারের প্রেক্ষিতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষণে আমরা এই দুই ব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করব। যথা,-
✳️রেলপথ ব্যবস্থা:-
(i) ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রতীক ছিল রেল ব্যবস্থা।
(ii) রেলপথ ব্যবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন এলাকা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।
(iii) রেলপথ বানানোর পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আদতে ভারতের উন্নতির কারণে রেলপথ বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি বরং উপনিবেশিক শাসনকে গতিশীল করাই ছিল রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য।
(iv) লর্ড ডালহৌসির আমলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প শুরু হয়।
✳️টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা:-
(i) উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রেলপথের মতোই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বিকাশ ঘটেছিল।
(ii) ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন টেলিগ্রাফ প্রযুক্তির ব্যবহারকে জরুরি করে তোলে।
(iii) বস্তুত রেলপথ ও টেলিগ্রাফের বিস্তার সহগামী হয়েছিল। রেলপথ বরাবর টেলিগ্রাফ লাইন তৈরি হয়।
(iv) এমনকি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে রেলস্টেশন গুলির মধ্যে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হতো। তার মধ্যে দিয়ে রেলের সিগন্যাল ব্যবস্থা কার্যকর করা যেত।
৫। কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে) :
ক) ধরো প্রথমবার তুমি রেলে চড়তে যাচ্ছ। রেলে চড়ার আগে এবং রেলে চড়ার পর তোমার অভিজ্ঞতা কেমন হয়েছে, তা বন্ধুকে চিঠি লিখে জানাও ৷
উত্তর : নিজে কর।
খ) ধরো তুমি ১৮৭০ -এর দশকে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের একজন বাসিন্দা। ঐ অঞ্চলের কৃষকদের তুলোচাষকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের বিবরণ তোমার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখো।
উত্তর : নিজে কর।
আরো পড়ুন
Class 8 History Chapter 3 Question Answer | ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রশ্ন উত্তর
Class 8 History Chapter 2 Question Answer | আঞ্চলিক শক্তির উত্থান প্রশ্ন উত্তর
Note: এই আর্টিকেলের ব্যাপারে তোমার মতামত জানাতে নীচে দেওয়া কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো। ধন্যবাদ।